দূরত্ব প্রায় সাড়ে ২২ কোটি কিমি। অথচ সেখানে পৌঁছোতে লাগবে মাত্র ৩০ দিন। ২১ শতকে এ ভাবেই চোখের পলকে লাল গ্রহ জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন রুশ মহাকাশ গবেষকেরা। তার জন্য তৈরি হয়েছে অতিশক্তিশালী অত্যাধুনিক ইঞ্জিন। মস্কোর মিশন সফল হলে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা নাসা (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) যে বড় ধাক্কা খাবে, তা বলাই বাহুল্য।সম্প্রতি মঙ্গল অভিযানের দিকে নজর দিয়েছে রুশ প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে একটি অতি শক্তিশালী প্লাজ়মা ইঞ্জিন তৈরি করেছেন সেখানকার মহাকাশবিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, এর সাহায্যে মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে পৌঁছোনো যাবে লাল গ্রহে। ইঞ্জিনটির নির্মাণকারী সংস্থা রোসাটম ট্রয়েটস্ক ইনস্টিটিউটের দাবি, তাঁদের যন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন যুগের সূচনা করবে। রোসাটমকে যাবতীয় সাহায্য করছে রাশিয়ার সরকারি মহাকাশ সংস্থা রসকসমস।

রুশ ইঞ্জিনটিতে ‘ম্যাগনেটো প্লাজমা প্রপালশান সিস্টেম’ ব্যবহার করেছেন মস্কোর গবেষকেরা। এতে হাইড্রোজেন আয়নের সাহায্যে তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করা হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত থ্রাস্ট সৃষ্টি করতে পারছে ওই ইঞ্জিন। এটি মহাকাশযান বহনকারী রকেটের গতিবেগ যে অনেকটাই বৃদ্ধি করবে, তা একরকম নিশ্চিত রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা।ইঞ্জিন নির্মাণকারী সংস্থা রোসাটম জানিয়েছে, এর সাহায্যে সেকেন্ডে ১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটবে মহাকাশযান। অর্থাৎ, ঘণ্টায় গতিবেগ দাঁড়াবে ৩.৬ লক্ষ কিমি। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানকে অন্তরীক্ষে পৌঁছে দিতে যে রকেট ব্যবহার করা হয়, সেগুলির সর্বোচ্চ গতিবেগ ৪.৫ কিলোমিটার/সেকেন্ড। সেই কারণেই চাঁদ বা মঙ্গলে পৌঁছোতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের।

রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা রসকসমসের তরফে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনটি নিয়ে সরকারি ভাবে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ওই ইঞ্জিন। সেখানে পাশ করলে বাণিজ্যিক ভাবে শুরু হবে এর উৎপাদন। সেটি অবশ্য যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ বলেই মনে করা হচ্ছে।
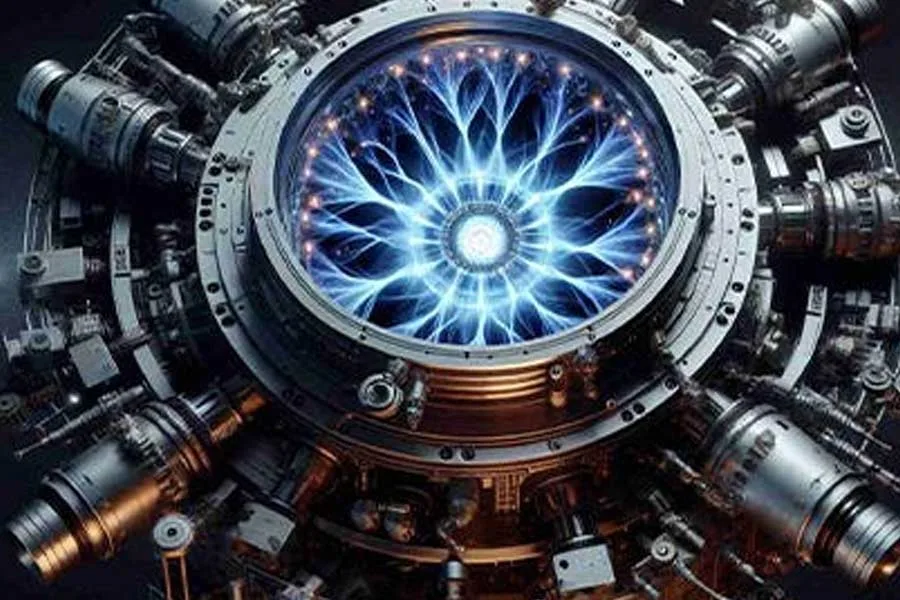
রুশ গবেষকদের এ হেন ইঞ্জিন তৈরির খবরে দুনিয়া জুড়ে পড়ে গিয়েছে হইচই। বিশ্লেষকদের দাবি, এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক জ্বালানি হিসাবে হাইড্রোজেনের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি বিশ্বের সবচেয়ে হালকা গ্যাস এবং বাতাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই ধরনের ইঞ্জিনের ব্যবহারে মহাকাশ গবেষণায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে বলে মনে করছেন তাঁরা।
মহাকাশ গবেষণায় প্লাজ়মা প্রপালশান পদ্ধতি নতুন নয়। তা সত্ত্বেও রোসাটমের ইঞ্জিনটিকে ‘খেলা ঘোরানো’ আবিষ্কার বলেই মনে করা হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ হল, রুশ ইঞ্জিনটির গতিবেগ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একাংশের মতে, ইঞ্জিনটির সাহায্যে নভোচারীরা মাত্র ৩০ দিনে মঙ্গলে পৌঁছে যেতে পারবেন। সেই মাইলফলককে অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হবে।
২০৩০ সালের মধ্যেই রোসাটম সংশ্লিষ্ট প্লাজ়মা ইঞ্জিনের একটি ফ্লাইট মডেল তৈরি করবে। এর পর সেটিকে মহাকাশে পাঠাবেন রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। সে ক্ষেত্রে সৌরজগতের বাইরে অভিযানের দরজাও খুলে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ ছাড়া দূরবর্তী গ্রহগুলিতে নভোচারী প্রেরণ এবং গ্রহাণু অনুসন্ধানের কাজ বেশ সহজ হবে বলে ইতিমধ্যেই দাবি করেছেন দুনিয়ার তাবড় মহাকাশবিজ্ঞানীরা।তবে রুশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের তৈরি প্লাজ়মা ইঞ্জিনের সামনে কোনও চ্যালেঞ্জ নেই, তা ভাবলে ভুল হবে। ইঞ্জিনটিকে নিয়ে রোসাটম যে দাবি করেছে, সেগুলির কতটা সত্যি তা যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। দ্বিতীয়ত মহাকাশযানের সঙ্গে ইঞ্জিনটিকে কী ভাবে যুক্ত করা হবে, তা এখনও স্পষ্ট করেননি রুশ বিজ্ঞানীরা। সেটি করা না গেলে ইঞ্জিনটিকে অন্তরীক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়।তৃতীয়ত, মহাশূন্যে নভোচারী পাঠালে প্রয়োজন হয় অফুরন্ত শক্তির। কারণ, মহাকাশযানের মধ্যে বিদ্যুতের প্রয়োজন রয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার সরবরাহ চালু রাখতে পারমাণবিক চুল্লির প্রয়োজন। সেটা এই ইঞ্জিন বহন করতে পারবে কি না, সেই পরীক্ষা এখনও চালানো হয়নিঅন্য দিকে মহাকাশ গবেষণায় রকেটযুগের ইতি ঘটাতে কোমর বেঁধে কাজ করছে নাসাও। কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণে এ বার থেকে ক্যাটাপল্ট ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সংস্থা। নতুন এই আবিষ্কার মহাকাশ গবেষণার সংজ্ঞা বদলাতে চলেছে বলে দাবি করা হয়েছে।মহাকাশ গবেষণায় বিপ্লব আনতে চলা ক্যাটাপল্টের আবিষ্কর্তা আমেরিকার ক্যালোফোর্নিয়াভিত্তিক স্টার্ট আপ স্পিনলঞ্চ। কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে দিতে রকেটের বদলি হিসাবে ওই যন্ত্র তৈরি করেছে তারা। সংস্থাটির দাবি, এর সাহায্যে ব্যাপক সস্তায় কোনও যান বা কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাশূন্যে পাঠানো যাবে। পাশাপাশি, ক্যাটাপল্ট পরিবেশবান্ধব হওয়ায় নেই কোনও দূষণের আশঙ্কা।স্পিনলঞ্চ জানিয়েছে, ক্যাটাপল্টের সাহায্যে হাইপারসোনিক গতিতে (শব্দের পাঁচ গুণের চেয়ে বেশি গতি) কৃত্রিম উপগ্রহ বা অন্তরীক্ষযান পৌঁছে যাবে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে। যন্ত্রটিতে রয়েছে ঘূর্ণায়মান দু’টি বিশাল হাতের মতো অংশ। এগুলির সাহায্যেই উৎক্ষেপণের পর গতির ঝড় তোলে ক্যাটাপল্ট।রকেটের মতো স্পিনলঞ্চের এই যন্ত্রে প্রয়োজন হচ্ছে না কোনও জ্বালানির। ক্যাটাপল্ট পুরোপুরি বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় এতে পরিবেশের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। ক্যালিফোর্নিয়ায় স্টার্ট আপ সংস্থাটি শুধু মুখেই যে একাধিক দাবি করেছে এমনটা নয়। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি পরীক্ষামূলক সফল উৎক্ষেপণও সেরে ফেলেছে স্পিনলঞ্চ।
এ-হেন ক্যাটাপল্ট যন্ত্রটির প্রেমে পড়ছেন নাসার তাবড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদেরা। আর তাই এয়ারবাস এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সঙ্গে মিলে এর উন্নত সংস্করণ তৈরির দিকে মন দিয়েছেন তাঁরা। সূত্রের খবর, ২০২৬ সালের মধ্যে ক্যাটাপল্টের সাহায্যে একগুচ্ছ কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থার।পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে কাটিয়ে মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযান নিয়ে যেতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড জ্বালানি পুড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করে রকেট। ক্যাটাপল্টের প্রযুক্তি এর থেকে একেবারে ভিন্ন। স্পিনলঞ্চ পেলোড (ওজন) উৎক্ষেপণের জন্য এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে বিশুদ্ধ গতিশক্তি। সংস্থার তৈরি যন্ত্রটিতে বিশাল ভ্যাকুয়াম সিলড সেন্ট্রিফিউজ় রয়েছে।ক্যাটাপল্ট উৎক্ষেপণের জন্য বিশেষ ধরনের একটি টিউব ব্যবহার করছে স্পিনলঞ্চ। এর সাহায্যে পেলোডগুলিকে অস্বাভাবিক গতিতে ঘুরিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা হচ্ছে। সেই শক্তিই কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানকে পৌঁছে দিচ্ছে অন্তরীক্ষে। পেলোডগুলিকে দুরন্ত গতিতে ঘোরাতেও বিদ্যুতের ব্যবহার করছে স্পিনলঞ্চ।











